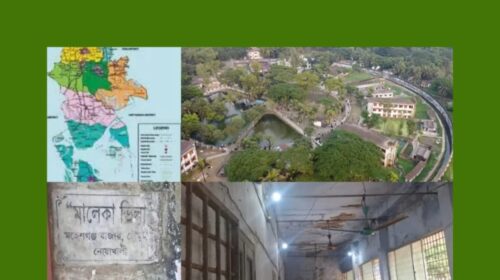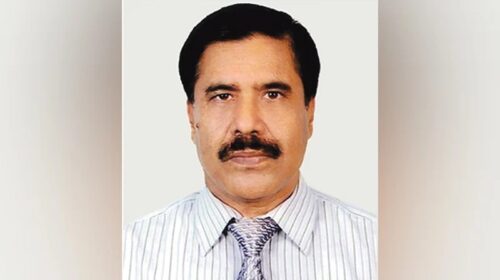বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ এক অদ্ভুত দ্বৈততার মধ্যে বন্দী। একদিকে সরকার শিক্ষার মানোন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের কথা বলছে; অন্যদিকে শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এমন সব শর্ত ও নিয়ম তৈরি করছে, যা যোগ্য শিক্ষকদের সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে।
সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে ১৭ বছরের অভিজ্ঞতাকে প্রধান শিক্ষক হওয়ার অন্যতম শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ‘অভিজ্ঞতার গ্যাঁড়াকল’ নিয়েই শিক্ষকদের মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র অসন্তোষ।অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কিন্তু যখন সেটি অযৌক্তিকভাবে দীর্ঘ করা হয়, তখন তা যোগ্যতার পথে এক অদৃশ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। অনার্স-মাস্টার্স ডিগ্রিধারী একজন শিক্ষক, যিনি দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত এবং প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন করেছেন, তিনি যদি ১৭ বছরের কম অভিজ্ঞতার কারণে প্রধান শিক্ষক হতে না পারেন, তবে তা নিছক অন্যায় নয়—এটি বৈষম্যও বটে।অন্যদিকে বাস্তবতা হলো, দেশে এমন বহু ব্যক্তি আছেন, যারা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা না করেও নীতিনির্ধারক, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, কিংবা সংসদ সদস্য হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন—তাদের অভিজ্ঞতার মানদণ্ড কী? একজন এমপি কি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ নিয়ে সংসদ পরিচালনা করেন? করেন না। অথচ শিক্ষক সমাজের নেতৃত্বে অভিজ্ঞতার নামে এক প্রকার প্রশাসনিক ‘শিকল’ চাপানো হয়েছে।বাংলাদেশে শিক্ষক সমাজের সবচেয়ে দীর্ঘদিনের এক দুঃখজনক বৈষম্য হলো “বিএড–নন–বিএড” বিভাজন। বিএড বা এমএড প্রশিক্ষণ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, তবে সেটিকে একমাত্র পদোন্নতির টিকিট বানানো কতটা যৌক্তিক? অনার্স-মাস্টার্স ডিগ্রিধারী একজন শিক্ষক যিনি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, শিক্ষণ কৌশল ও শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ—তার বেতন গ্রেড বা পদোন্নতির পথে বিএড সনদকে বাধা বানানো আসলে এক ধরনের প্রশাসনিক নির্যাতন।
সরকারি বিদ্যালয়ে বিএড ছাড়াই অনার্সধারীরা ১০ম গ্রেডে যোগদান করেন, কিন্তু বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একই যোগ্যতা নিয়েও নন–বিএড শিক্ষকরা ১১শ গ্রেডে পড়ে থাকেন। এটি শুধুই সংখ্যার পার্থক্য নয়, এটি মর্যাদার ও সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যও সৃষ্টি করে।
এভাবে একই কারিকুলামে পড়ানো দুই শিক্ষককে আলাদা গ্রেডে রাখার মধ্য দিয়ে সরকার কার্যত শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণিভেদ তৈরি করছে—যা শিক্ষার মানোন্নয়নেরবাংলাদেশে বেশিরভাগ শিক্ষক পেশায় প্রবেশ করেন ত্যাগ ও ভালোবাসা থেকে। তারা খুব দ্রুত প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবতা, পাঠদান কৌশল ও প্রশাসনিক দায়িত্ব শিখে ফেলেন।
তবু ৪-৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলেও তাদের বলা হচ্ছে, “তুমি এখনো অযোগ্য প্রধান শিক্ষক হওয়ার জন্য।” ১৭ বছরের অভিজ্ঞতার শর্ত তাই কেবল সময়ের অপচয় নয়, এটি এক ধরনের পেশাগত অবমূল্যায়ন।
এখানে প্রশ্ন আসে—“অভিজ্ঞতা” কি শুধুই সময়ের হিসাব? নাকি সেটি কার্যকর নেতৃত্ব, দক্ষতা ও একাডেমিক মানদণ্ডের ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত? শিক্ষকদের মূল্যায়নে যদি কেবল ‘বয়স’ ও ‘সময়কাল’ নির্ধারক হয়, তবে সেখানে তরুণ মেধাবীদের জন্য কোনো জায়গাই থাকবে না। শিক্ষকদের পদোন্নতিতে অভিজ্ঞতা নির্ভর নীতি নতুন নয়। অতীতে স্বাশিপ (স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদ)–এর প্রভাবের সময়েও তিন বছরের অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রধান শিক্ষক হওয়ার সুযোগ বন্ধ করা হয়েছিল।
এতে বহু মেধাবী শিক্ষক প্রশাসনিক নেতৃত্বের সুযোগ হারিয়েছেন। এই প্রথা শিক্ষাক্ষেত্রে একরকম “অভ্যন্তরীণ স্বৈরাচার” তৈরি করেছে। যেখানে নেতৃত্ব নির্ধারণ হয় না মেধা, একাডেমিক সনদ বা প্রশিক্ষণ দিয়ে, বরং ‘কত বছর পার করেছো’—এই প্রশ্নে।
ফলাফল হিসেবে, যারা দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করলেও নতুন চিন্তাধারা, সৃজনশীল শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বা প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা চালু করার মতো মনোভাব রাখেন না, তারাও কেবল অভিজ্ঞতার কারণে নেতৃত্বে চলে আসেন। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে পড়ে স্থবির, উদ্যমহীন ও সংস্কারবিমুখ। বাংলাদেশে বেসরকারি শিক্ষকদের অবস্থা বরাবরই অবহেলিত। তারা দেশের সর্বাধিক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিচ্ছেন, অথচ তাদের বেতন, পদোন্নতি ও সামাজিক মর্যাদা সরকারি শিক্ষকদের তুলনায় অনেক কম।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হতে হলে যত শর্তই থাকুক না কেন, সেখানে অন্তত পদোন্নতির সুযোগ আছে। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষকরা এমপিওভুক্ত না হলে প্রাথমিকভাবে কোনো নিরাপত্তাই পান না। তাদের জন্য ১৭ বছরের অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক করা মানে এক প্রকার ‘প্রশাসনিক শাস্তি’।
বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন এখনও স্বতন্ত্র নয়। শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে যারা বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে আসেন, তারা প্রশাসনিকভাবে অনেক ক্ষমতাবান হলেও শিক্ষাক্ষেত্রের প্রকৃত বাস্তবতা থেকে দূরে।
শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ড, মন্ত্রণালয়—সব জায়গায় এদের আধিপত্য। বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষকরা যেখানে পদোন্নতির আশা নিয়ে বসে আছেন, সেখানে বিসিএস কর্মকর্তারা নীতি নির্ধারণ করছেন—যা এক প্রকার কাঠামোগত বৈষম্য। অন্যদিকে প্রশাসন ক্যাডার ও পুলিশ ক্যাডারের চোখে শিক্ষা ক্যাডাররা আবার নিচু স্তরের কর্মকর্তা! এই স্তরভিত্তিক মানসিকতা আসলে পুরো শিক্ষা কাঠামোকেই বিভক্ত ও দুর্বল করে দিচ্ছে।
শিক্ষা ব্যবস্থায় নেতৃত্ব নির্বাচনে অভিজ্ঞতা অবশ্যই বিবেচ্য, কিন্তু সেটি যেন মেধা, সনদ, প্রশিক্ষণ ও পারফরম্যান্সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়
চাকরির প্রস্তুতি গাইডএকজন প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান হওয়ার জন্য যদি একাডেমিকভাবে উচ্চ ডিগ্রি (অনার্স-মাস্টার্স), পেশাগত প্রশিক্ষণ (বিএড, এমএড), কো-কারিকুলাম সার্টিফিকেট এবং অন্তত ৫-৭ বছরের কার্যকর অভিজ্ঞতা থাকে, তবে সেটিই যথেষ্ট বিনোদন সংবাদএছাড়া নেতৃত্বমূলক পদে নিয়োগের আগে একটি বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ (Educational Leadership Training) চালু করা যেতে পারে। এটি হলে কেউ বয়সে তরুণ হলেও নেতৃত্বে পরিপক্ব হতে পারবেন, এবং অভিজ্ঞরাও তাদের প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়াতে পারবেন।
সবচেয়ে বড় বৈষম্য তৈরি হয়েছে শিক্ষকদের বেতন কাঠামোয়। আজও বাংলাদেশে শিক্ষকদের জন্য আলাদা, স্বতন্ত্র বেতন স্কেল নেই। সরকারি কর্মকর্তারা যেখানে নিয়মিত ইনক্রিমেন্ট ও সুযোগ-সুবিধা পান, সেখানে শিক্ষকরা মাসের শেষে বেতন পেতেই হিমশিম খান।অনার্স-মাস্টার্স ডিগ্রিধারী শিক্ষক ১১শ গ্রেডে পড়ে থাকেন, অথচ কম যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য ক্যাডারের কর্মকর্তারা ৯ম বা ৮ম গ্রেডে পৌঁছে যান। এখানে সরকার একপ্রকার নীরব দর্শক। তারা শিক্ষা সংস্কার, পাঠ্যক্রম পরিবর্তন, বা পরীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে যত আলোচনা করেন, শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা নিয়ে ততটা চিন্তা করেন না।কিন্তু ইতিহাস বলে—যে দেশ শিক্ষককে মর্যাদা দেয়, সেই দেশই দ্রুত উন্নত হয়।
বাংলাদেশে শিক্ষা সংস্কারের মূল শর্ত হওয়া উচিত—শিক্ষকের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা। অভিজ্ঞতার নামে বৈষম্য, বিএড-নন-বিএড বিভাজন, বেসরকারি-সরকারি বৈষম্য—এসবের অবসান না ঘটলে শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নয়।
একজন শিক্ষক যদি নিজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত দেখে পড়ানোর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন, তবে শিক্ষার্থীরাও সেই অনুপ্রেরণা হারায়।
অভিজ্ঞতা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেটি যেন কোনো শিক্ষকের স্বপ্নকে পঙ্গু না করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত এখনই নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করা—যাতে যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ, একাডেমিক দক্ষতা ও নেতৃত্বগুণই হয় প্রধান শিক্ষক হওয়ার আসল মানদণ্ড; ক্যালেন্ডারের বছর নয়।
শিক্ষাকে যদি আমরা জাতির মেরুদণ্ড বলি, তবে সেই মেরুদণ্ডে বারবার বৈষম্যের ভার চাপিয়ে তাকে নত করা নয়—বরং শক্তিশালী করাই আমাদের দায়িত্ব।