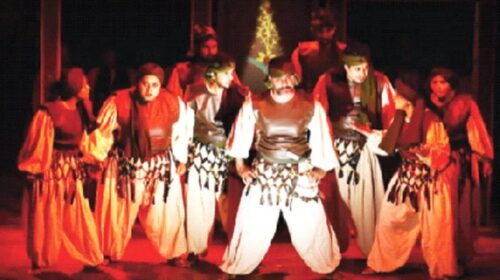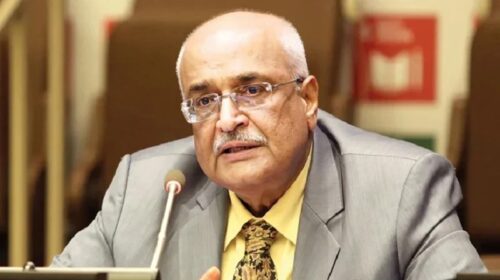দেশজুড়ে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রস্তাব ও জুলাই চার্টার নিয়ে ঐকমত্য গড়ে তুলতে বাংলাদেশে গঠিত হয় জাতীয় ঐকমত কমিশন (এনসিসি)। সম্প্রতি কমিশন তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবিত সংস্কার বাস্তবায়নের রোডম্যাপ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান এখনো অস্পষ্ট। এমনকি দলগুলোর মধ্যে গভীর বিভাজন রয়ে গেছে।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) অভিযোগ করেছে, জুলাই চার্টার বিষয়ে তাদের ভিন্নমত বা ‘নোট অব ডিসেন্ট’ কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এছাড়া যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে- পরবর্তী সংসদ ‘সংবিধান সংস্কার পরিষদ’ হিসেবে গঠিত হবে। এ বিষয়ে কমিশনের সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি বলেও অভিযোগ করেছে দলটি।
এ বছর ১৭ই অক্টোবর ২২টি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিতে ‘জুলাই চার্টার’ জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয়। এটি ‘নতুন বাংলাদেশ’-এর যাত্রার সূচনা হিসেবে ঘোষিত হয়। কারণ এনসিসি বেশিরভাগ সংস্কার প্রস্তাবে ঐকমত্য গড়ে তুলেছিল। তবে, ছাত্রনেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি (এনসিপি) এবং পাঁচটি বামপন্থী দল এই চার্টারে সই করেনি। এনসিপি জানিয়েছে, চার্টার বাস্তবায়নের একটি স্পষ্ট রোডম্যাপ ছাড়া তারা কোনো নথিতে সই করবে না।বামপন্থী দলগুলো- বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাসদ (মার্কসবাদী) এবং বাংলাদেশ জাসদ মত দিয়েছে যে চার্টারে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- প্রতিফলিত হয়নি। এসব সংশোধন না হলে তারা সই করবে না।
গণফোরাম, যারা শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল, তারাও চার্টারে সই করেনি।
রাজনৈতিক বিভাজন
বিএনপি চায় গণভোট (রেফারেন্ডাম) ও জাতীয় নির্বাচন একই দিনে হোক। কিন্তু জামায়াতে ইসলামি চায়, গণভোটটি জাতীয় নির্বাচনের আগেই হোক। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ- যাদের দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ও তাদের মিত্র জাতীয় পার্টিকে পরামর্শ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেয়া হয়। মোট ৩৪টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে এনসিসি ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব দেয়। যার বিপরীতে ৫৮টি ভিন্নমত যুক্ত করা হয়। তার বেশিরভাগই বিএনপি, বাম দল ও জামায়াতের পক্ষ থেকে আসে।
জুলাই চার্টারের মূল বিষয়সমূহ
চার্টারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। তবে এতে এমন কিছু সংস্কার রয়েছে, যা সংবিধান সংশোধন ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে- ২৭টি নির্বাচন সংস্কার, ২৩টি বিচার বিভাগীয় সংস্কার, ২৬টি প্রশাসনিক সংস্কার, ২৭টি দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত সংস্কার। গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে- সংসদে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হতে হবে, প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা পুনর্বিন্যাস করতে হবে, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ দুই দফায় সীমিতকরণ করতে হবে, দলীয় চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী পদ একসঙ্গে না রাখার বাধ্যবাধকতা থাকবে, বিচারব্যবস্থা, পুলিশ, দুর্নীতি দমন কমিশন ও নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ করতে হবে।চার্টারে বলা হয়েছে, আগামী সংসদ ২৭০ দিনের মধ্যে যদি চার্টারটি পাস না করে, তবে সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হবে। বিএনপি এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কারণ সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা শুধুমাত্র প্রেসিডেন্টের।
তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃপ্রবর্তন
চার্টারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল। এই সরকার নির্বাচনের সময় অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন হিসেবে কাজ করবে এবং এর প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে নির্বাচনের জন্য পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হবে। প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রধান বিচারপতির অবসরের বয়স বাড়ানোর মাধ্যমে ২০০৬ সালে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা দুর্বল করে দেয়। পরে সেই বিচারপতি দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানান এবং বিএনপি প্রেসিডেন্টকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করে দেয়, যা প্রক্রিয়া-বহির্ভূত ছিল। পরে ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ এই ব্যবস্থা বাতিল করে। যার ফলে তিনটি বিতর্কিত নির্বাচন হয়। এর মধ্যে বিএনপি কেবল ২০১৮ সালের নির্বাচনে অংশ নেয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃপ্রবর্তন দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের বেশিরভাগ দলের প্রধান দাবি। পাকিস্তানেও অনুরূপ একটি পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থা রয়েছে, যদিও সেখানে ঐকমত্য পাওয়া কঠিন
মূল অচলাবস্থা
বর্তমানে দুটি বড় প্রশ্ন রাজনৈতিক ঐকমত্যে বাধা সৃষ্টি করেছে। তা হলো গণভোটের সময়কাল। বিএনপি চায়, গণভোট জাতীয় নির্বাচনের দিনেই হোক। জামায়াত ও এনসিপি চায়, নির্বাচনের আগে হোক। গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট পাওয়া গেলে তবেই চার্টার কার্যকর হবে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো অনুপাতভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা (পিআর সিস্টেম)। জামায়াত, অন্যান্য ইসলামপন্থী দল ও এনসিপি মনে করে এই পদ্ধতি সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াবে। কিন্তু বিএনপি চায় প্রথমে ভোটে জয়ী পদ্ধতি বহাল থাকুক। কারণ অনুপাতভিত্তিক ভোটব্যবস্থা ছোট দলগুলোকে শক্তিশালী করবে এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাড়াবে বলে তারা মনে করে।
নতুন রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল অর্ডার (আরপিও) অনুযায়ী প্রতিটি দলকে নিজেদের প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করতে হবে, যা বাংলাদেশের প্রচলিত রাজনৈতিক জোট ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।
উপসংহার
দলের ভেতরের বিভাজনই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরকে জটিল করে তুলেছে। আওয়ামী লীগকে পুরোপুরি বাদ দেয়া মানে দেশের একটি বড় অংশের রাজনৈতিক মতামতকেও উপেক্ষা করা। দলটি যে জনঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, তা সত্য। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেছে- ‘নতুন বাংলাদেশ’-এর নির্মাণে আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মত কি উপেক্ষিত থাকবে, নাকি এটি আবারও এক ‘অসমাপ্ত বিপ্লব’-এর অধ্যায় হয়ে উঠবে?